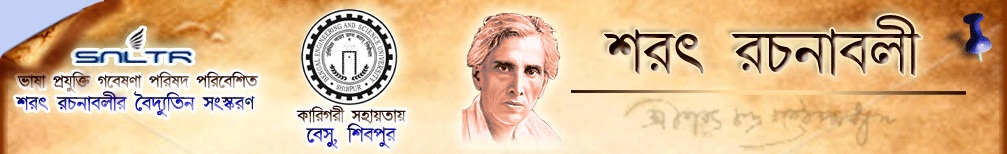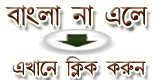রস-সেবায়েৎ
শ্রীযুক্ত 'আত্মশক্তি'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—
আপনার ৩০ শে ভাদ্রের 'আত্মশক্তি' কাগজে মুসাফির-লিখিত 'সাহিত্যের মামলা' পড়িলাম। একদিন বাংলা-সাহিত্যে সুনীতি-দুর্নীতির আলোচনায় কাগজে কাগজে অনেক কঠিন কথার সৃষ্টি হইয়াছে, আর অকস্মাৎ আজ সাহিত্যের 'রসে'র আলোচনায় তিক্ত রসটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এমনিই হয়। দেবতার মন্দিরে সেবকের পরিবর্তে 'সেবায়েতে'র সংখ্যা বাড়িতে থাকিলে দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়ে না, কমিয়াই যায়, এবং মামলা ত থাকেই।
আধুনিক সাহিত্যসেবীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বহু কুবাক্য বর্ষিত হইয়াছে। বর্ষণ করার পুণ্যকর্মে যাঁহারা নিযুক্ত, আমিও তাঁহাদের একজন। ‘শনিবারের চিঠি’র পাতায় তাহার প্রমাণ আছে।
মুসাফির-রচিত এই 'সাহিত্যের মামলা'র অধিকাংশ মন্তব্যের সহিতই আমি একমত, শুধু তাঁহার একটি কথায় যৎকিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।
রবীন্দ্রনাথের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ জানেন, কিন্তু আমার নিজের কথা যতটা জানি তাহাতে শরৎচন্দ্র 'কল্লোল', 'কালি-কলম' বা বাংলার কোন কাগজই পড়েন না বা পড়িবার সময় পান না, মুসাফিরের এ অনুমানটি নির্ভুল নয়। তবে, এ কথা মানি যে, সব কথা পড়িয়াও বুঝি না, কিন্তু না-পড়িয়াও সব বুঝি, এ দাবী আমি করি না।
এ ত গেল আমার নিজের কথা। কিন্তু যা লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে সে জিনিসটি যে কি, এবং যুদ্ধ করিয়া যে কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে সে আমার বুদ্ধির অতীত।
রবীন্দ্রনাথ দিলেন সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়া, এবং নরেশচন্দ্র দিলেন সেই ধর্মের সীমানা নির্দেশ করিয়া। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনই যুক্তি, পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, ব্যস্, ইহার পরে আর কথা চলিবে না। কিন্তু অনেক কথাই চলিল। তখন কে জানিত কাহার সীমানায় কে পা বাড়াইয়াছে এবং সেই সীমানার চৌহদ্দি লইয়া এত লাঠি-ঠ্যাঙ্গা উদ্যত হইয়া উঠিবে। আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় 'সীমানা বিচারে'র রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাপার।
| এই ওয়েবসাইটটি সবচেয়ে ভালো ভাবে দেখতে হলে Mozilla Firefox, Microsoft Edge অথবা Apple Safari browser ব্যবহার করুন। | ||||||||
|
|
 |
|||||||